নবম – ৯ শ্রেণি সাধারণ গণিত ২য় অধ্যায় অনুশীলনী ২.১ সমাধান
প্রয়োজনীয় তথ্য:
সেট : বাস্তব বা চিন্তা জগতের সু-সংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে। সেটকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর A,B,C, …………. X,Y,Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
সেটের প্রত্যেক বস্তু বা সদস্যকে সেটের উপাদান (element) বলা হয়। যেমন: B = {a,b} হলে, B সেটের উপাদান a এবং b.
সেট প্রকাশের পদ্ধতি : সেটকে প্রধানত দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। যথা : h_v : (১) তালিকা পদ্ধতি এবং (২) সেট গঠন পদ্ধতি
(১) তালিকা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দ্বিতীয় বন্ধনী { } এর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং একাধিক উপাদান থাকলে ‘কমা’ ব্যবহার করে উপাদানগুলোকে আলাদা করা হয়। যেমন: A = {a,b}, B = {2,4,6}, C = { নিলয়, তিশা, শুভ্রা } ইত্যাদি।
(2) সেট গঠন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে উপাদান নির্ধারণের জন্য সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে। যেমন : A = {x : x স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যা }, B = {x : x নবম শ্রেণির প্রথম পাঁচজন শিক্ষার্থী } ইত্যাদি।
বিভিন্ন প্রকার সেট :
সসীম সেট : যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায়, তাকে সসীম সেট বলে।
অসীম সেট : যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না, তাকে অসীম সেট বলে।
ফাঁকা সেট : যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে। ফাঁকা সেটকে Φ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
ভেনচিত্র : জন ভেন (১৮৩৪-১৮৮৩) চিত্রের সাহায্যে সেট প্রকাশ করার রীতি প্রবর্তন করেন। এতে বিবেচনাধীন সেটগুলোকে সমতলে অবস্থিত বিভিন্ন আকারের জ্যামিতিক চিত্র যেমন আয়তাকার ক্ষেত্র, বৃত্তাকার ক্ষেত্র এবং ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়। জন ভেনের নামানুসারে চিত্রগুলো ভেন চিত্র নামে পরিচিত।
উপসেট : কোনো সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায়, তাদের প্রত্যেকটি সেটকে ঐ সেটের উপসেট বলা হয়।
প্রকৃত উপসেট : B যদি A এর উপসেট হয় এবং A এর অন্তত একটি উপাদান সেটে না থাকে তাহলে B কে A এর প্রকৃত উপসেট বলা হয় এবং B ⊆ A লেখা হয়। যেমন : A = {3,4,5,6} এবং B = {3,5} দুইটি সেট।
সেটের সমতা : দুইটি সেটের উপাদান একই হলে, সেট দুইটিকে সমান বলা হয়। যেমন : A = {3,5,7} এবং B = {5,3,7) দুইটি সমান সেট এবং A = B চিহ্ন দ্বারা লেখা হয়।
সেটের অন্তর : কোনো সেট থেকে অন্য একটি সেট বাদ দিলে যে সেট গঠিত হয় তাকে বাদ সেট বা সেটের অন্তর বলে।
সার্বিক সেট : বাস্তব আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকল সেট একটি নির্দিষ্ট সেটের উপসেট। সেটটি
যেমন : A = {x,y} সেটটি B = {x,y,z} এর একটি উপসেট। এখানে, B সেটকে A সেটের সাপেক্ষে সার্বিক সেট বলে।
| পূরক সেট : U সার্বিক সেট এবং A সেটটি U এর উপসেট। A সেটের বহির্ভত সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে A সেটের পূরক সেট বলে। A এর পূরক সেটকে Ac বা A´ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। গাণিতিকভাবে Ac = U \ A |
সংযোগ সেট : দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে সংযোগ সেট বলা হয়।
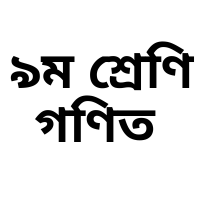
| ছেদ সেট : দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ছেদ সেট বলে। মনে করি, A ও B দুইটি সেট। A ও B এর ছেদ সেটকে A ∩ B দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পড়া হয় A ছেদ B বা A intersection B। সেট গঠন পদ্ধতিতে A ∩ B = {x : x ∈ A এবং x ∈ B }
নিশ্চেদ সেট : দুইটি সেটের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তবে সেট দুইটি পরস্পর নিশ্চেদ সেট। |
শক্তি সেট : A সেটের শক্তি সেটকে P(A) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
ক্রমজোড় : একজোড়া উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রথম অবস্থানে আর কোনটি দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে, তা নির্দিষ্ট করে জোড়া আকারে প্রকাশকে ক্রমজোড় বলা হয়।
কার্তেসীয় গুণজ : A ও B যেকোনো সেটের উপাদানগুলোর সকল ক্রমজোড়ের সেটকে তাদের কার্তেসীয় গুণজ সেট বলে।
অন্বয় (Relation) : যদি A ও B দুইটি সেট হয় তবে সেটদ্বয়ের কার্তেসীয় গুণজ A × B সেটের অন্তর্গত ক্রমজোড়গুলোর অশূন্য উপসেট R কে A সেট থেকে B সেটের একটি অন্বয় বা সম্পর্ক বলা হয়।
ফাংশন (Function) : যদি দুইটি চলক x এবং y এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যেন x এর যেকোনো একটি মানের জন্য y এর একটিমাত্র মান পাওয়া যায়, তবে x কে y এর ফাংশন বলা হয়।
ডোমেন (Domain) ও রেঞ্জ (Range) : কোনো অন্বয়ের ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানসমূহের সেটকে এর ডোমেন এবং দ্বিতীয় উপাদানসমূহের সেটকে এর রেঞ্জ বলা হয়। মনে করি, A সেট থেকে B সেটে R একটি অন্বয় অর্থাৎ R ⊆ A × B । R এ অন্তর্ভুক্ত ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানসমূহের সেট হবে R এর ডোমেন এবং দ্বিতীয় উপাদানসমূহের সেট হবে R এর রেঞ্জ। R এর ডোমেনকে ডোম R এবং রেঞ্জকে রেঞ্জ R লিখে প্রকাশ করা হয়।
ফাংশনের লেখচিত্র (Graph) : ফাংশনের চিত্ররূপকে লেখচিত্র বলা হয়। ফাংশনের ধারণা সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে লেখচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। পরস্পর লম্বভাবে ছেদী সরলরেখা দুইটিকে অক্ষরেখা এবং অক্ষদ্বয়ের ছেদ বিন্দুকে মূলবিন্দু বলে।
উলম্ব অক্ষ (Perpendicular Axes) : কোনো সমতলে পরস্পর লম্বভাবে ছেদী দুইটি সরলরেখা XOX´ এবং YOY´ আঁকা হলো। অনুভূমিক রেখা XOX´ কে x -অক্ষ, উলম্ব রেখা YOY´ কে y – অক্ষ এবং অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দু O কে মূলবিন্দু (Origin) বলা হয়।
স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) : দুইটি অক্ষের সমতলে অবস্থিত কোনো বিন্দু থেকে অক্ষদ্বয়ের লম্ব দূরত্বের যথাযথ চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলা হয়।
সৃজনশীল প্রশ্ন – ১
ƒ(x) = x2 + 4x + 3
A = {x ∈ Ι : x বিজোড় সংখ্যা এবং x < 6}
B = {x∈ Ι : x, 21 এর গুণনীয়ক} এবং
C = {x ∈ Ι : x, 7 এর গুণিতক এবং x < 35}.
ক. ƒ(−1) এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. দেখাও যে, A – এর উপাদান সংখ্যা n হলে, P(A)- এর উপাদান সংখ্যা 2n কে সমর্থন করে। ৪
গ. দেখাও যে, A× (B ∩ C) = (A × B) ∩ (A ×C) ৪
সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
(ক) দেওয়া আছে, ƒ(x) = x2 + 4x + 3
∴ ƒ(− 1) = (− 1)2 + 4. (− 1) + 3
= 1 − 4 + 3 = 0 (Ans.)
(খ) দেওয়া আছে, A = {x ∈ Ι : x বিজোড় সংখ্যা এবং x < 6}
= {1, 3, 5}
A সেটের উপসেট সমূহ : {1}, {3}, {5}, {1, 3}, {1, 5}, {3, 5}, {1, 3, 5}, Æ
∴ P(A) = {{1}, {3}, {5}, {1, 3}, {1, 5}, {3, 5}, {1, 3, 5}, Æ}
A সেটের উপাদান সংখ্যা ৩ এবং এর শক্তি সেট P(A) এর উপাদান সংখ্যা = 8 = 23
ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজের প্রকারভেদ
সুতরাং A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে P(A) এর উপাদান সংখ্যা 2n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)
(গ) দেওয়া আছে, B = {x ∈ Ι : x, 21 এর গুণনীয়ক}
= {1, 3, 7, 21}
এবং C = {x ∈ Ι : x, 7 এর গুণিতক এবং x < 35}
= {7, 14, 21, 28}
এখন, B ∩ C = {1, 3, 7, 21} ∩ {7, 14, 21, 28} = {7, 21}
বামপক্ষ = A × (B ∩ C) = {1, 3, 5} × {7, 21}
= {(1, 7), (1, 21), (3, 7), (3, 21), (5, 7), (5, 21)}
আবার, A × B = {1, 3, 5} × {1, 3, 7, 21}
= {(1, 1), (1, 3), (1, 7), (1, 21), (3, 1), (3, 3), (3, 7), (3, 21), (5, 1), (5, 3), (5, 7), (5, 21)}
A × C = {1, 3, 5} × {7, 14, 21, 28}
= {(1, 7), (1, 14), (1, 21), (1, 28), (3, 7), (3, 14), (3, 21), (3, 28), (5, 7), (5, 14), (5, 21), (5, 28)}
ডানপক্ষ = (A × B) ∩ (A × C)
= {(1, 7), (1, 21), (3, 7), (3, 21), (5, 7), (5, 21)}
∴ A × (B ∩ C) = (A × B) ∩ (A × C). (দেখানো হলো)
সৃজনশীল প্রশ্ন – ২
g(x) = \frac{3x + 1}{3x – 1} এবং h(t) = \frac{t^4 + t^2 + 1}{t^2} দুইটি বীজগাণিতিক রাশি।
ক. g(0) এবং h(1) এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. \frac{g\frac({1}{x}) +1}{g\frac({1}{x}) – 1} এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, h(t^2) = h(\frac{1}{t^2}) ৪
২ নং প্রশ্নের সমাধান
(ক) দেওয়া আছে, g(x) = \frac{3x + 1}{3x – 1}
⸫ g(0) = \frac{3.0 + 1}{3.0 – 1}
= \frac{0 + 1}{0 – 1}
= \frac{1}{– 1}
= – 1 (Ans.)
এবং h(t) = \frac{t^4 + t^2 + 1}{t^2}
h(1) = \frac{1^4 + 1^2 + 1}{1^2}
= \frac{1+ 1+ 1}{1}
= \frac{3}{1}
= 3
(খ) পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ২.২ এর উদাহরণ ২৪ এর অনুরূপ।
(গ) দেওয়া আছে, h(t) = \frac{t^4 + t^2 + 1}{t^2}
⸫ h (t^2) = \frac{(t^2)^4 + (t^2)^2 + 1}{(t^2)^2}
= \frac{t^8 + t^4 + 1}{t^4}
এবং h(\frac{1}{t^2}) = \frac{(\frac{1}{t^2})^4 + (\frac{1}{t^2})^2 + 1}{(\frac{1}{t^2})^2}
= \frac{\frac{1}{t^8} + \frac{1}{t^4} + 1}{\frac{1}{t^4}}
= \frac{\frac{1 + t^4 + t^8}{t^8} }{\frac{1}{t^4}}
= \frac{1 + t^4 + t^8}{t^4}
⸫ h(t^2) = h(\frac{1}{t^2}) (প্রমাণিত)